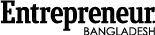আজকের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) বুম আসলে ডট-কম বুদবুদের পুনরাবৃত্তি — এবং পতনের সময় খুব দূরে নয়।
শ্রীনিবাস রাও
৯০-এর দশকের শেষ দিকে, আমি যখন ক্যালিফোর্নিয়ার বার্কলেতে ছাত্র ছিলাম, তখন চোখের সামনে ইন্টারনেট বাণিজ্যের উন্মাদনা চলছিল। স্রেফ প্রতিষ্ঠানের নামের শেষে “.com” বসালেই বিনিয়োগকারীরা মিলিয়ন ডলার ঢালতেন।
কোনও ব্যবসায়িক মডেল ছাড়াই কোম্পানিগুলো সুপার বোল বিজ্ঞাপন দিচ্ছিল। অনেকে একরাতে কাগুজে কোটিপতি হয়ে যাচ্ছিল। ১৯৯৯ সালে সান মাইক্রোসিস্টেমস-এ ইন্টার্ন করার সময় আমি যখন ১০১ হাইওয়ে দিয়ে যেতাম, তখন রাস্তার পাশে একটার পর একটা বিলবোর্ড — AltaVista, Excite, Netscape — সেসব কোম্পানি যেগুলো কয়েক বছরের মধ্যেই ইতিহাস হয়ে গেল।
২০০১-এর দিকে সেই দালানগুলো হয়ে উঠল ফাঁকা, মরুভূমির মতো নীরব।
আর আজ — ২৫ বছর পর — আমরা যেন একই চক্রে ফিরে এসেছি।
কেবল নাম বদলেছে। তখন ছিল “.com”, এখন সেটা “AI-powered”। আজকের অধিকাংশ AI স্টার্টআপ শুধু প্রযুক্তির ওপর চটকদার কোট পরিয়েছে — কিন্তু ভিতরে নিজেদের কিছুই নেই।
এ যেন এক আধুনিক কার্ডের ঘর
দেখুন খোলাসা করে বলি:
স্টার্টআপগুলো নির্ভর করছে OpenAI-এর ওপর।
OpenAI নির্ভর করছে Microsoft-এর ক্লাউড (Azure)-এর ওপর।
Microsoft নির্ভর করছে NVIDIA-এর ওপর।
আর NVIDIA নিয়ন্ত্রণ করছে সেই চিপস যা পুরো AI ইকোসিস্টেম চালায়।
অর্থাৎ একটি স্টার্টআপের ভিত্তি এমন একটি প্রযুক্তির ওপর দাঁড়িয়ে, যেটার মালিক সে নিজে না — এবং যার ব্যাকএন্ড আরও তিন-চারটি বড় প্রতিষ্ঠানের ওপরে নির্ভরশীল।
এই কাঠামো আসলে তাসের ঘর। একটিও স্তম্ভ যদি পড়ে যায় — দাম, নীতিমালা, বা জিওপলিটিক্সের কারণে — সবকিছু ভেঙে পড়বে।
বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বিপদের সংকেত
বাংলাদেশেও আজ অনেক উদ্যোক্তা বা স্টার্টআপ নিজেদের AI-ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে দাবি করছে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে — তারা কী নিজেরা কোনও AI মডেল তৈরি করছে? না কি ChatGPT বা ওপেন সোর্স মডেলের ওপর একটি ইউজার ইন্টারফেস বসিয়ে দিচ্ছে?
তাদের অধিকাংশেরই:
নিজস্ব ডেটা নেই
নিজস্ব অ্যালগরিদম নেই
স্কেল করার কোনো কৌশল নেই
শুধু বিদেশি API-এর ওপর নির্ভর করে কিছু ডেমো বানিয়ে তাতে বিনিয়োগ আনছে — যা খুব বেশি দিন টিকবে না।
বিনিয়োগকারীদের অন্ধ আস্থা
আমরা এখন দেখছি এক অদ্ভুত রকমের প্রতিযোগিতা — যেখানে মূল লক্ষ্য হচ্ছে ‘ব্যবহারকারী প্রথমে টানো, রাজস্ব পরে ভাবা যাবে।’ ঠিক যেমনটা হয়েছিল ডট-কম যুগে।
এখানে বাস্তবতা হচ্ছে, এখনকার AI ব্যবস্থাপনা চালাতে খরচ অনেক বেশি। শুধু মডেল ট্রেইনিং নয়, সার্ভারে চালানোর খরচও অগ্নিমূল্য।
ফলে যারা এখন কিছু ফ্রি দিচ্ছে, তারা টিকবে না — কারণ তারা ব্যবসার মৌলিক নিয়মেই টিকে থাকতে পারবে না।
সবাই ভাঙবে না — কেউ কেউ টিকবেও
২০০০ সালের ডট-কম বুদবুদের পর Google, Amazon-এর মতো কোম্পানি টিকে গিয়েছিল। তেমনি AI খাতেও কিছু প্রতিষ্ঠান টিকে যাবে। যাদের নিজস্ব প্রযুক্তি থাকবে, নিজস্ব ডেটাসেট থাকবে — তারা ভবিষ্যতের নেতৃত্ব দেবে।
কিন্তু বাকিরা? তারা হয় বন্ধ হয়ে যাবে, না হয় অন্য কোম্পানির হাতে বিক্রি হবে।
উপসংহার: আশার মাঝে হুঁশিয়ারি
AI কোনো ভুয়া প্রযুক্তি নয়। কিন্তু বর্তমান AI স্টার্টআপ সংস্কৃতি এক ধরনের বুদবুদের মতো — যা কখন ফেটে যাবে বলা মুশকিল।
বাংলাদেশে যারা AI নিয়ে কাজ করছেন বা বিনিয়োগ করছেন, তাদের এখনই নিজস্ব প্রযুক্তি, ডেটা সংগ্রহ এবং দীর্ঘমেয়াদি কৌশলের দিকে মনোযোগ দিতে হবে। না হলে ২০২৬-এর আগে তাদের নামটাও আর কেউ মনে রাখবে না।
চলমান প্রযুক্তি বিপ্লবে টিকে থাকতে চাইলে শোরগোল নয়, চাই সত্যিকারের উদ্ভাবন।